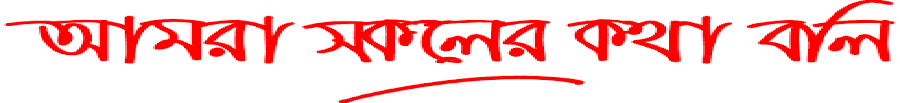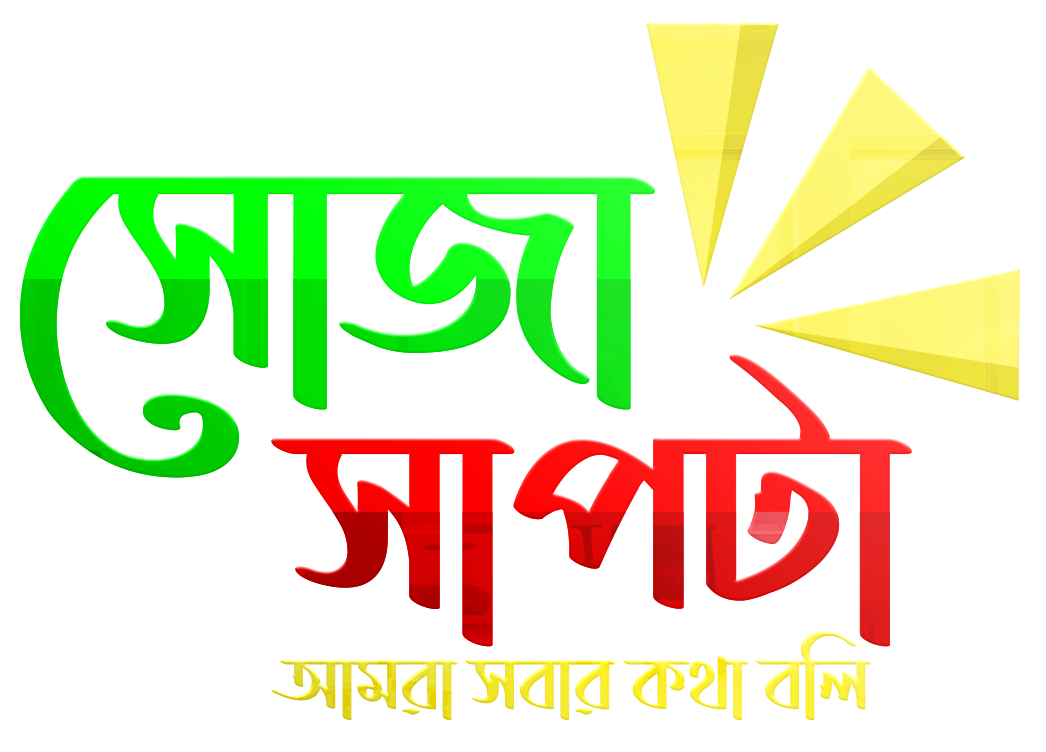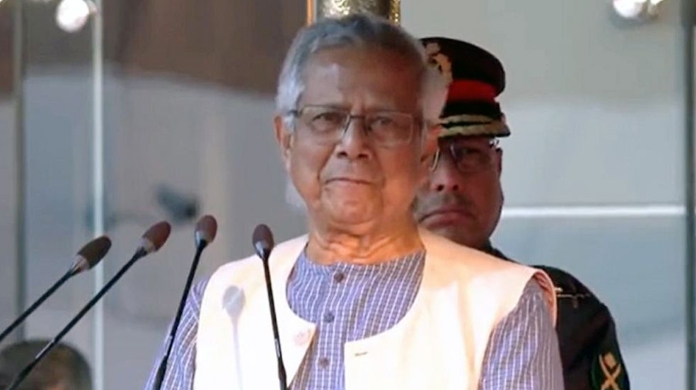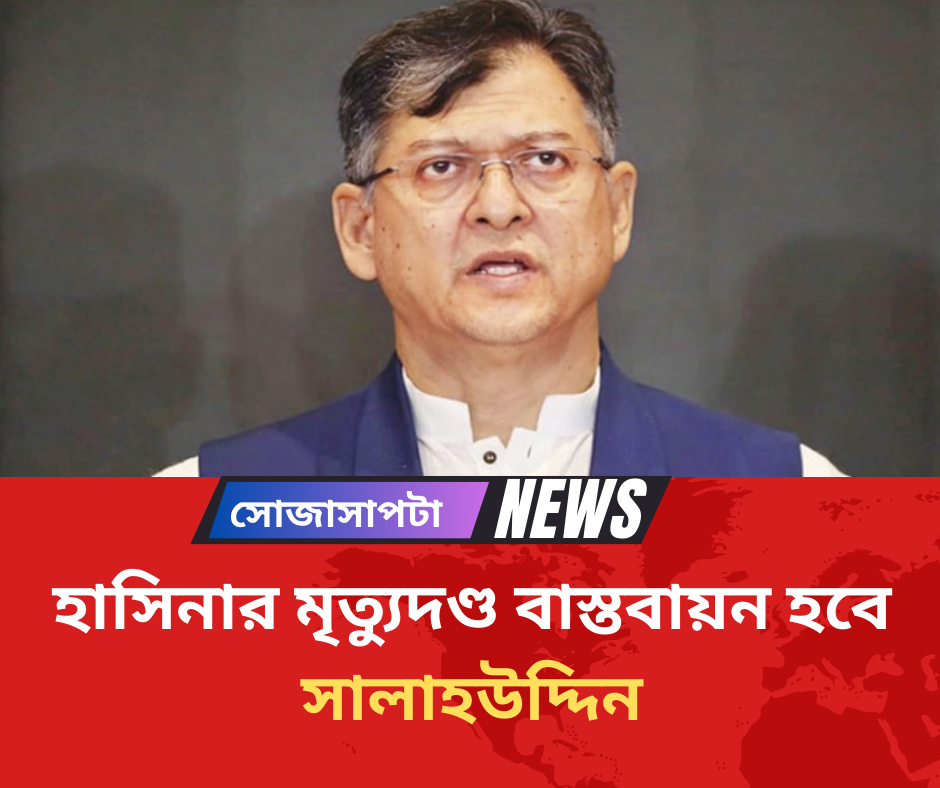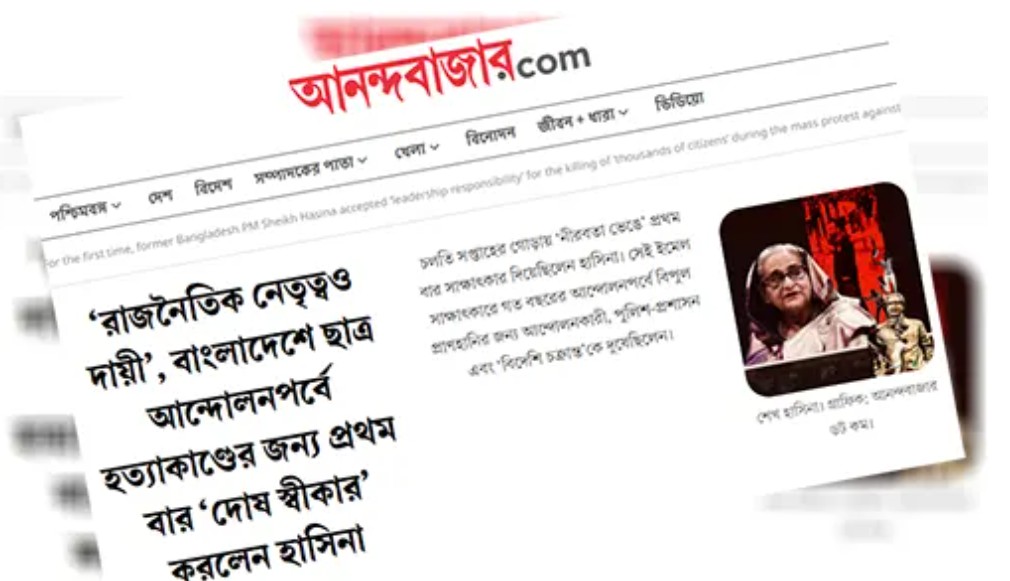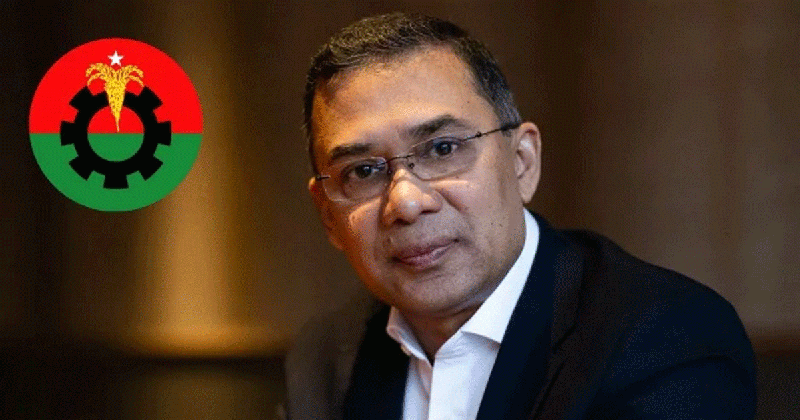পুরনো ভবনকে যেসব উপায়ে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করা যায়

- আপডেট সময় : ০৬:৪৫:৩১ অপরাহ্ন, শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫
- / ৮ জন পড়েছেন
ঢাকায় ফের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শনিবার বিকাল ৬টার পর এ কম্পন অনুভূত হয়।
এর আগে শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৬ মিনিটে ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে ঢাকা ও সিলেট। গত দুই মাসের মধ্যে ঢাকায় এনিয়ে তিনবার ভূমিকম্প হলো।
ভূমিকম্পে সবচেয়ে ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও ভূমিকম্প বিষয়ক বিল্ডিং কোড না মানা। এ বছর তুরস্ক ও সিরিয়ার ভুমিকম্পে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পেছনে সেই কারণই উঠে এসেছিলো।
বড় ভূমিকম্পে ঘনবসতি শহর ঢাকার ভয়াবহতা কতটা হতে পারে তার একটি চিত্র উঠে এসেছে রাজউকের আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্টের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায়।
তাদের হিসেবে টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ধসে পড়তে পারে সাড়ে ৮ লাখের বেশি অর্থাৎ প্রায় ৪০% স্থাপনা। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার বা আড়াই লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। আবার সিলেটের ডাউকি চ্যুতিরেখায় ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকায় ধসে পড়তে পারে প্রায় ৪১ হাজার স্থাপনা।
তবে একটা ভবনকে যদি ভূমিকম্প সহনীয় করে গড়ে না তোলা হয়, এরপরও কিছু উপায় আছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রকৌশলীরা ভবনকে ভূমিকম্প সহনীয় করতে পারেন।
বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদি আহমেদ আনসারী জানিয়েছিলেন এমন সাতটি প্রযুক্তি সম্পর্কে। এর তিনটি খুব উঁচু ভবনের ভবনের জন্য যেগুলো খুব বেশ ব্যয়বহুল, আর অন্য চারটি সাধারণ ভবনের জন্য।
প্রচলিত চারটি উপায়
যেভাবে সাধারণ ভবনকে ভূমিকম্পের জন্য মজবুত করা হয়, যেগুলোকে রেট্রোফিটিং বলা হয়। এগুলো দেখতে খুবই সহজ মনে হলেও যদি একজন প্রকৌশলী এর সাথে যুক্ত না থাকেন তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী কিভাবে করতে হবে সেটি নির্ধারণ করা যাবে না।
প্রকৌশলীরা প্রথমে ভবনের বিভিন্ন অংশে কেটে পরীক্ষা করে দেখবেন ভেতরে কী অবস্থা।এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন। রেট্রোফিটিং সাধারণত যেসব উপায়ে করা হয় যার ছবি দিয়েছেন ড. আনসারী।

কলাম জ্যাকেটিং (ছবিতে সর্ব বামে)
কলাম বা পিলারকে জ্যাকেট পরিয়ে দেয়ার মতো উপায় এটি। অর্থাৎ পিলারগুলোকে যা আছে তার চেয়ে আরো মোটা করে দেয়া যেন সেটি আরো শক্তিশালী হয়। অনেক সময় বিশেষায়িত উপকরণও দিয়েও এটি করা হয়।
শিয়ার ওয়াল
শিয়ার ওয়ালে পিলারের পাশে আরো রড দিয়ে ঢালাই করে একটি দেয়ালের মতো তোলা হয়। এটি আংশিক হতে পারে (যেমন ছবিতে দ্বিতীয়) অথবা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে (যেমন ছবিতে তৃতীয়) তবে ভবনের কোন কোন অংশে করতে এটা করা সম্ভব সেটাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
স্টিল ব্রেসিং (ছবিতে চতুর্থ)
এক্ষেত্রে দুই পিলারের মাঝখানে একটি ধাতব ফ্রেম বসানো হয় যেটি ভুমিকম্পের ঝাঁকুনি থেকে পিলারকে রক্ষা করতে পারে। এটি ঠিক ছবির মত না হয়ে কোণাকুণি বরাবরও হতে পারে।
ওয়াল থিকেনিং
এক্ষেত্রে দুই কলামের মাঝের দেয়ালটাকেই মোটা করে ওজন বাড়িয়ে নেয়া হয়। এটিও রড ব্যবহার করে ঢালাইয়ের মত প্রক্রিয়ায় করা হয়।
উন্নত বিশ্বের তিন প্রযুক্তি
টিএমডি (টিউন মাস ড্যাম্পার)
এক্ষেত্রে ভবনের ছাদের দিকে বড় আকারের একটি সিস্টেম বসানো হয়। এর ভেতরে তেল বা পানির মতো তরল পদার্থ থাকে। সেটা এমনভাবে করা হয় যেন বসানো সিস্টেমটি নিজে দুলে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি শোষণ করতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে এর ভেতরের তরল পদার্থ দুলবে, আবার কোনো ক্ষেত্রে সিস্টেমটাই ডানে-বামে স্লাইড করবে।
আরেকভাবেও এটা করা যায় সেটা পেন্ডুলামের মতো। সেক্ষেত্রে তরল পাদার্থবিশিষ্ট বিশেষ পেন্ডুলামও ঝাঁকির সাথে দুলে ভবনের নড়াচড়া কমাতে পারে।
এটা ভবনের উপরে বিশালাকারের হতে পারে যেমন তাইওয়ানের তাইপেই ওয়ান ও ওয়ান। এটি ১০১ তলা একটি ভবন যেখানে এমন বড় পেন্ডুলাম ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশে এখনো কোথাও এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়নি বলে জানান ড. আনসারী।
তবে পেন্ডুলাম আরেকভাবেও ব্যবহার হয় বিমের মাঝে, তবে সেটিকে ঠিক এই টিএমডি প্রযুক্তি না, বরং বেজ আইসোলেটরের মধ্যে ফেলা হয়।
বেজ আইসোলেটর
বেজ আইসোলেটর প্রযুক্তি বসানো হয় ভবনের নিচ দিয়ে যেটি ভবনকে ভিত্তি থেকে আলাদা করে দেয়। এটিকে এমনভাবে সেট করা হবে যেনো ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে নিচের অংশটি নড়বে, কিন্তু উপরের অংশ দুলবে না।
সেটি সহজভাবে বুঝতে ধরুন একটি বাক্সের নিচে এমনভাবে চাকা বা বল বসালেন যেন তার নিচে দুললে চাকাটি এদিক-ওদিক নড়বে, কিন্তু চাকার উপরে বাক্স পর্যন্ত সেই দুলুনি যাবে না।
এটি অনেক ক্ষেত্রে তেলভিত্তিক পেন্ডুলাম দিয়েও করা হয়। উন্নত বিশ্বে অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালকে নিরাপদ করতে এটি করা হয়। বাংলাদেশে কোনো ভবনে এই প্রযুক্তি ব্যবহার না করা হলেও যমুনা ব্রিজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানান ড. আনসারী।
বিআরবি (বাকলিং রিস্ট্রেইন্ড ব্রেইস)
বিআরবিও একটি অতি ব্যয়বহুল প্রযুক্তি। সহজে বুঝালে স্টিল ও স্প্রিঙের মতো একটি কাঠামো যেটি সংকোচন-প্রসারণে সক্ষম। ভুমিকম্পে এর ভেতরের স্প্রিং-এর সংকোচন-প্রসারণ হয় এবং সেটি পিলারের উপর চাপ না ফেলে নিজে কাঁপুনি শোষণ করে। এটি সাধারণত আমেরিকা বা চীনে তৈরি হওয়ায় সেখানেই বেশি ব্যবহার হয়।
তবে এসব প্রযুক্তিই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এজন্য ভবন তৈরির পরের চেয়ে আগেই মাটি ও ভবন সংক্রান্ত বিষয়ে ভুমিকম্পের দিক বিবেচনা করে ভবন নির্মানটাই বেশি যৌক্তিক।
নিরাপদ ভবন নির্মাণে যা খেয়াল রাখতে হবে
বাংলাদেশে নিরাপদ, শক্তিশালী এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধী কাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন। ভৌগোলিকভাবে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের বড় বড় শহর ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে রয়েছে।
অপরিকল্পিত নগরায়ণ ছাড়াও পুরোনো, দুর্বল কাঠামোগত ভবন এই ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য একটি কার্যকর বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।
একটি শক্তিশালী ও ভূমিকম্প–সহনীয় নগরী গড়ে তুলতে হলে নতুন ভবন নির্মাণে নজর দিতে হবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও সামগ্রিক প্রস্তুতি গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
তথ্যসূত্র: বিবিসি বাংলা